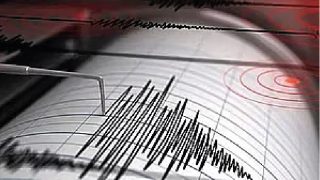দু’টি জিনিসের জন্য (সৃষ্টিকর্তার কাছে) আমি খুবই কৃতজ্ঞ : এক. আমি উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং দুই. উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছি। এই দু’টি জিনিস আমাকে আমার মতো করে তৈরি করেছে। নেহাত একটি সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার বিনিময়ে একে আমি বিকিয়ে দিতে পারি না। তবে এর পরও কথা আছে। কথা হলো এই যে, কিভাবে আমি আজকের ‘আমি’তে পরিণত হলাম।
দু’টি জিনিসের জন্য (সৃষ্টিকর্তার কাছে) আমি খুবই কৃতজ্ঞ : এক. আমি উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং দুই. উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছি। এই দু’টি জিনিস আমাকে আমার মতো করে তৈরি করেছে। নেহাত একটি সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার বিনিময়ে একে আমি বিকিয়ে দিতে পারি না। তবে এর পরও কথা আছে। কথা হলো এই যে, কিভাবে আমি আজকের ‘আমি’তে পরিণত হলাম।
আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা উত্তর কোরিয়ার হাইসান শহরে। ছোট শহর। লাখ দুয়েক মানুষের বসত এ শহরে। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইয়ালু নদী। উত্তর কোরিয়া ও চীন দু’দেশের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে নদীটি। আর ভয়ানক ঠাণ্ডা এ শহরটি। এটিকে বলা হয় ‘উত্তর কোরিয়ার সবচেয়ে শীতল শহর’। এর তাপমাত্রা কখনো কখনো মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে যায়।
মা ও বাবা দু’জনেরই খুব আদরের ছিলাম আমি। তারা একেবারে শিশুকাল থেকেই আমাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখিয়েছেন। বাবা মাঝে মাঝে আমাকে তার কোলে বসিয়ে শিশুদের বই পড়িয়ে শোনাতেন। তবে রূপকথার বই নয়। রূপকথার বই উত্তর কোরিয়ায় পাওয়া যায় না। এদেশে বই প্রকাশ করতে পারে কেবল সরকার এবং সেসব বই রাজনৈতিক বিষয় দিয়ে ঠাসা। রূপকথা নেই, রাজপুত্র ও রাজকন্যা নেই, রাক্ষসখোক্ষস নেই, কী আছে তবে সেসব বইতে? আছে দক্ষিণ কোরিয়া নামের এক ‘ভয়াল’ দেশের কথা। ওই দেশে শিশুদের থাকার জন্য বাড়ি নেই, তারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে। তাদের পায়ে এমনকি জুতোও নেই।
আমাদের আরো পড়তে হতো আমাদের নেতাদের কথা যে, এই নেতারা আমাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন। বইয়ে লেখা ছিল, আমাদের প্রিয় নেতা কিম জং ইল-এর আছে অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছাশক্তির জোরে আবহাওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিম ইল সুং ইউনিভার্সিটিতে তিন বছর পড়াশোনাকালে তিনি দেড় হাজার বই লিখেছিলেন ইত্যাদি।
শুধু বই নয়, কিমপূজার এই আতিশয্য ছড়িয়ে পড়ে সবগুলো মিডিয়ায়। এ নিয়ে বানানো হয় প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্র এবং টিভি শো। সেসব নিয়মিতই দেখানো হয় দেশের একমাত্র টিভিকেন্দ্রে, যেটির নিয়ন্ত্রণভার সরকারের হাতে। যখনই টিভি পর্দায় নেতাদের ছবি ভেসে উঠত, সাথে বেজে উঠত আবেগসঞ্চারী সুরলহরী। অন্য অনেকের মতো সেই আবেগ আমার ভেতরটাকেও ছুঁয়ে যেত। আসলে পিতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা উত্তর কোরিয়ার সংস্কৃতি। আর আমাদের সবার কাছে কিম ইল সুং ছিলেন প্রিয় দাদু এবং কিম জং ইল আমাদের পিতা।
উত্তর কোরিয়ায় শিশুদের একেবারে শুরু থেকেই নিয়ম করে শেখানো হয় দেশের শত্রুদের ঘৃণা করতে। আমাদের স্কুল ও পাঠ্যবইগুলো ছিল আমেরিকানদের কি¤ভূতকিমাকার ছবিতে ভর্তি। নীল চোখ ও বড় নাকওয়ালা ছবির মানুষগুলো নিরপরাধ মানুষদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে। স্কুলে মাঝে মাঝে আমাদের সারি ধরে দাঁড় করানো হতো। আমাদের সামনে থাকত মার্কিন সৈন্যের মূর্তি। আমরা সেগুলো ছুরি মেরে ও পিটিয়ে ‘হত্যা’ করতাম। মোটের ওপর, স্কুলে পাঠ্য প্রতিটি বিষয়েই কিছু-না-কিছু রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা ঢুকিয়ে দেয়া হতো। যেমন গণিতের একটি প্রশ্ন এরকম : ‘যদি তুমি একজন মার্কিন বেজন্মাকে হত্যা করো এবং তোমার সঙ্গী করে দু’জনকে, তাহলে তোমাদের কাছে কতজন আমেরিকান বেজন্মার লাশ থাকল?’
এ ছাড়া এমন অনেক কিছু ছিল, যা করা, কেনা ও বিক্রি করা ছিল নিষিদ্ধ। আনুগত্য শেখানোর এবং অবাধ্যতার পরিণাম শিক্ষা দিতে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। আমি যখন একেবারে ছোট, তখনকার একটা ঘটনা বলি। এক তরুণকে গ্রেফতার করা হলো। তার অপরাধ, সে একটা গরু জবাই করে তার গোশত খেয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় গরু হলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি এতই দামি যে, তাকে কিছুতেই জবাই করে খাওয়া যাবে না। কেননা, গরু দিয়ে চাষবাস করতে হয়, সে গাড়িও টানে।
যা হোক, গ্রেফতারকৃত যুবকটির কথা বলছিলাম। সে যক্ষ্মায় ভুগছিল এবং তার ঘরে খাওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। কিন্তু পুলিশ এসব কথায় ভুলবে কেন? তারা যুবকটিকে একটি মার্কেটের পেছনে নিয়ে গেল এবং একটি কাঠের সাথে শক্ত করে বাঁধল। এরপর তিন ব্যক্তি রাইফেল দিয়ে তাকে গুলি করতে থাকল। যতক্ষণ না যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, ততক্ষণ গুলি চলল। দৃশ্যটি আমার মা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি ভীষণ মর্মাহত হন। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে, তার নিজ দেশে একটি প্রাণীর জীবনের চেয়ে একজন মানুষের জীবনের মূল্য এত কম।
সিনেমা দেখা নিয়েও উত্তর কোরিয়ায় চলে মজার কাণ্ড। সরকারিভাবে তৈরি করা প্রচারণামূলক চলচ্চিত্র দেখতে কোনো নিষেধ নেই। কিন্তু ওগুলো ভীষণ একঘেয়ে। কাজেই চোরাইপথে আসা বিদেশী মুভি ও টিভি শোর চাহিদা বিপুল। পুলিশের ভয়কে তুড়ি মেরেই মানুষ ঘরে ঘরে ওসব দেখে। এ নিয়েও চলে মজাদার ইঁদুর-বেড়াল খেলা। যেমন কোনো বাড়িতে ডিভিডিতে বিদেশী ছবি বা টিভি অনুষ্ঠান চলছে জানতে পেলেই পুলিশ হানা দেয়। তারা এসে প্রথমেই বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যাতে বাড়ির লোকজন ডিভিডি প্লেয়ার থেকে ক্যাসেটটি বের করে নিতে না পারে। লোকজনও কম যায় না। তারা পুলিশের কৌশল ঠেকাতে পাল্টা কৌশল হিসেবে দু’টি ডিভিডি প্লেয়ার রাখতে শুরু করে। পুলিশ আসার খবর পেলেই তারা আসলটি সরিয়ে ফেলে।
আমার কাকার একটি ভিসিআর ছিল। হলিউডের সিনেমা দেখার জন্য আমি প্রায়ই তার বাড়িতে যেতাম। সিনেমা শুরুর আগেই কাকী দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বলতেন, ‘চুপচাপ দেখতে থাকো। কেউ একটি শব্দও করবে না।’ আমার পছন্দের ছায়াছবি ছিল সিনডারেলা, স্নো হোয়াইট এবং জেমস বন্ড সিরিজ। তবে যে ছায়াছবিটি আমার জীবন বদলে দেয় সেটি হলো টাইটানিক। আমি কল্পনাও করতে পারি না যে, এরকম সলজ্জ প্রেমের কোনো ছায়াছবি উত্তর কোরিয়ায় নির্মিত হতে পারে। কেউ বানালে অবশ্যই তার মৃত্যুদণ্ড হতো। আমি চমৎকৃত হতাম দেখে যে, ছবির চরিত্রগুলো প্রেমের জন্য মরতে রাজি, আমাদের মতো শাসকগোষ্ঠীর জন্য নয়। মানুষের চিন্তার এই স্বাধীনতা, যা কি না তাদের গন্তব্য পছন্দ করার অধিকার দেয়, তা আমাকে খুবই টানত। টাইটানিক ছবিটি আমাকে একটুখানি হলেও প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে শেখায়।
দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
২০০৭ সালের মার্চ মাসে ইয়নমাই ও তার মা এক চোরাচালানিকে কিছু টাকা দেন। বিনিময়ে ওই চোরাচালানি তাদের ইয়ালু নদী পার করে চীনে পৌঁছে দেবে। তাদের এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল দু’টি। প্রথমত, একটি নিপীড়ক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পালানো এবং দ্বিতীয়ত, ইয়নমাইর বড় বোনকে খুঁজে বের করা। সে সপ্তাহখানেক আগে দেশ ছেড়ে পালিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া চলে গেছে। মা ও মেয়ে চীনে পা দিয়েই বিপদে পড়ে গেল। চোরাচালানিরা মাকে এক চাষির কাছে স্ত্রী ও চাকরানি হিসেবে বিক্রি করে দিলো। আর ১৩ বছর বয়সী ইয়নমাই হয়ে গেল এক চোরাচালানির সহকারী ও দাসী। এভাবে বছর দুই কাটানোর পর মা-মেয়ের মিলন ঘটল। ২০০৯ সালে তারা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের একটি গোপন মিশনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। এই মিশনটি তাদেরকে চীন ছাড়তে এবং গোবি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মঙ্গোলিয়া পৌঁছাতে সাহায্য করে। মঙ্গোলিয়া থেকে অবশেষে মা ও মেয়ে দক্ষিণ কোরিয়া পৌঁছে যায়।
তখন শীতকাল। তাপমাত্রা নেমে এসেছে মাইনাস ২৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। আমাদের দলটি রাতের বেলা হেঁটে চীন সীমান্ত অতিক্রম করছে। শীতের রাতে সীমান্ত পাড়ি দেয়ার একটা সুবিধা হলো, প্রচণ্ড শীতের কারণে সীমান্তে প্রহরা থাকে ঢিলেঢালা। তারপরও আমাদের ধরা পড়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল শতভাগ। মা ও আমি ঠিক করেছিলাম, আমরা কিছুতেই ওদের হাতে ধরা পড়ব না। তাই মা নিয়েছিলেন বেশ কিছু স্লিপিং পিল। ধরা পড়লেই ওগুলো গিলে ফেলবেন তিনি। আর আমার জ্যাকেটের পকেটে ছিল একটি রেজর ব্লেড। ধরা পড়ার মুখোমুখি হলেই ওটি নিজের গলায় চালিয়ে দেবো। ওরা আমাদের আর জীবন্ত দেশে ফেরত পাঠাতে পারবে না।
আমরা চলছিলাম কখনো বাসে, কখনো ট্রেনে। এভাবে গোবি মরুভূমিতে পৌঁছতে লেগে গেল চার দিন। আমাদের সাথে ছিলেন চীনের হান গোত্রের এক পুরুষ। খ্রিষ্টান মিশনটিতে কাজ করতেন তিনি। তিনি আমাদের বললেন, ‘যদি আপনাদের কেউ ধরা পড়ে যান, প্লিজ, দলের অন্যদেরও ধরিয়ে দেবেন না। পুলিশকে বলবেন, আপনি একাই যাচ্ছেন। তাহলে অন্যরা বেঁচে যাবে।’
গাইড এবার আমাদের নিয়ে এলেন গোবি মরুভূমির মাঝখানে একটি শহরে। খ্রিষ্টান মিশনের এক নারী আমাদের দুটো ফ্ল্যাশলাইট ও দুটো কম্পাস দিয়েছিলেন। দলের একমাত্র পুরুষ সদস্যটিকে সেগুলোর ব্যবহার শিখিয়ে দিলেন গাইড। এবার আমাদের যেতে হবে উত্তর-পশ্চিম দিকে। সীমান্তের মূল উঁচু বেড়া পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই পাঁচটি কাঁটাতারের বেড়া ডিঙাতে হবে আমাদের। সীমান্ত পার হওয়ার পর প্রথম যে মানুষটির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে তাকে নিজেদের পরিচয় দিতে ‘উত্তর কোরিয়ান শরণার্থী’ বলে।
সূর্যাস্তের পরই একটি ট্যাক্সি আমাদের নিয়ে এলো শহর থেকে কয়েক মাইল দূরের এক জায়গায়। এবার আমাদের চৈনিক গাইড তার শেষ নির্দেশনা দিলেন : ‘মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে দূরে যে উজ্জ্বল আলোকমালা দেখতে পাবেন, ওটা মঙ্গোলিয়ার এক শহরের। ওই আলো ধরে এগিয়ে যাবেন। যে আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছে, ওগুলো চীনের। সাবধান, ওদিকে পা বাড়াবেন না।’ বলেই তিনি আঙুল তুলে উজ্জ্বল আলোকমালা দেখিয়ে দিলেন। আবার বললেন, ‘আর শুনুন, কেউ যদি কখনো দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন অথবা কম্পাস ব্যবহার করতে না জানেন, তাহলে আকাশে তারা খুঁজে বের করবেন। যেদিকে তারা দেখা যাবে, ওটাই উত্তর।’
এরপরই গাইড বিদায় হলেন। আমরাও চলতে শুরু করলাম। কয়েক পা গিয়েই পেছনে ফিরে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য অভিভূত করল আমি ও আমার মাকে। দেখলাম, প্রচণ্ড শীতল মাঠে হাঁটু গেড়ে বসেছেন আমাদের গাইড, প্রার্থনা করছেন আমাদের নিরাপদ যাত্রা। এক অজানা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার হৃদয়মন। কে এই মানুষ, যিনি আমাদের ভাষাটি পর্যন্ত জানেন না, তিনি কেন আমাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন? আমার মনের গহিনে ধন্যবাদসূচক নিঃশব্দ প্রার্থনা গুঞ্জরিত হতে থাকল।
আমরা হেঁটে চলেছি মরুভূমির ওপর দিকে। মরুভূমি মানেই তো মাইলের পর মাইল বালু, নুড়িপাথর আর রোদে পোড়া ঘাসের আভাস। চলতে চলতে মনে হলো, এখানে শীত বুঝি জীবন্ত কোনো প্রাণী। এই প্রাণীটি আমার শরীরে কামড় বসাচ্ছে। আর আমার পা আঁকড়ে ধরছে, যাতে আমার চলার গতি কমে যায়। শীত কমানোর জন্য আমি মায়ের গা ঘেঁষে চলতে থাকলাম। তারপরও আমার কাঁপুনি না থামায় মা তার কোটটি আমাকে দিয়ে দিলেন। মায়ের জুতো জোড়াটি ছিল খুবই পাতলা, তাই বারবার নুড়িপাথরের গুঁতো খেতে থাকলেন তিনি। তা দেখে আমাদের দলের একমাত্র পুরুষ মানুষটি তার অতিরিক্ত রানিং সু জোড়া মাকে দিলেন। পরতে গিয়ে দেখা গেল, ওগুলো মায়ের পায়ের চেয়ে অনেক বড়। মা ওগুলোর ফিতে এমনভাবে বাঁধলেন, যাতে জুতোগুলো পায়ে আটকে থাকে।
ওই রাত ছিল আমার জীবনের দীর্ঘতম রাত। প্রতি মুহূর্তে আমরা ভাবছিলাম, এই বুঝি একটা শব্দ শুনব অথবা দূরে হেডলাইটের আলো দেখতে পাব। ভাবছিলাম আর আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা চতুর্থ কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে গা মুচড়ে মুচড়ে পার হচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি ইঞ্জিনের শব্দ আর দেখি বিপুল সার্চলাইট গোটা মরুভূমিকে আলোকিত করে ফেলেছে। আমরা তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং ওই আলো ও শব্দ চলে না যাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকলাম।
কয়েক ঘণ্টা পর শীত আরো জেঁকে বসল। পাশাপাশি আমার মনে জেঁকে বসল এক অচেনা আতঙ্ক, আমরা সত্যিই দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছতে পারব তো? আমার মনের ভেতর নানা রকম ভাবনা খেলা করতে লাগল। মনে হলো, আমি এবার মরে যাবো। আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই, কেউ কি আমার কবর খুঁজে পাবে, নাকি আমি এমনভাবে বিস্মৃত হবো যে, আমি কোনো দিন, কোনোকালে ছিলামই না।
এবার আমি মনে মনে কিম জং ইলকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। কিন্তু প্রিয় নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা খুবই কঠিন কাজ। এরকম কাজ আমি আগে কখনো করিনি। আমার মনে হলো, তার দুই হাত যেন আমাকে অনুসরণ করছে এবং চেষ্টা করছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে (কী আশ্চর্য, পরে মা আমাকে বলেন ওই সময় তিনিও ঠিক ওই ভাবনাটিই ভাবছিলেন)।
এ সময় বলা নেই কওয়া নেই কোত্থেকে একদল বন্যপ্রাণী আমাদের ঘিরে ফেলল। ওগুলো হাঁপাচ্ছিল। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। এবার আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, ‘কেউ কি আছেন? আমাদের একটু সাহায্য করুন।’ কিন্তু কোথাও কেউ ছিল না।
আমি শুয়ে পড়ার এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম। হঠাৎ আমরা একটি ট্রেনের শব্দ শুনলাম। মনে হলো, খুব কাছেই। আমাদের দলের সবাই তখন দৌড়ে পালিয়েছে। আমি ও মা দৌড় লাগালাম আরেক দিকে। কয়েক মিনিট পরই আধো-অন্ধকারে আমরা দেখতে পেলাম সীমান্তের বেড়া। এই বেড়ার মাঝে মাঝে বড় বড় ছিদ্র আর তাতে বেড়া অতিক্রমকারীদের কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো লেগে আছে। আমরা যখন বেড়া ডিঙাতে গেলাম, তখন কাঁটাতারে আমার কোটের কিছু অংশও ছিঁড়ে গেল, যেন ওই বেড়াটি আমাকে চীনে রেখে দেয়ার চেষ্টা করছে। আমরা অবশেষে মুক্ত হলাম। আমাদের পেছন দিকে ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে, মরুভূমিতে আমাদের দীর্ঘ ছায়া পড়ছে। আমার মা আমার হাত ধরে রেখেছেন। আমরা এখন মঙ্গোলিয়ায়।
অবশেষে দক্ষিণ কোরিয়ায়
মঙ্গোলিয়ায় সৈন্যরা এই দুই নারীকে প্রথমে একটি ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর পর তাদের দক্ষিণ কোরিয়াগামী একটি বিমানে তুলে দেয়া হয়। সিউলে আবার আটক করা হয় তাদের। তারা গুপ্তচর কি না যাচাই করতে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর পাঠানো হয় একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে। সেখানে ক’দিন কাটে তাদের। তারপর দক্ষিণ কোরিয়ার একটি ছোট শহরে পুনর্বাসন করা হয় তাদের। সেখানে পড়াশোনায় ফিরে যায় ইয়নমাই। কলেজে ওঠে সে। এই সময়, ২০১৩ সালে হারানো বোনের সাথে পুনর্মিলন হয়।
২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব যুব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ডাবলিন যায় ইয়নমাই। যুবনেতাদের এই বার্ষিক সভায় ইয়নমাই প্রতিনিধিত্ব করে নিজ দেশ উত্তর কোরিয়ার। তার পরিকল্পনা ছিল, সম্মেলনে সে চীনে মানবপাচার বিষয়ে বক্তৃতা দেবে। তবে নিজেও যে পাচার হয়েই এসেছে, এটি প্রকাশ করবে না।
নিজেকে নিয়ে আমার সবচেয়ে বড় ভয়টি হলো, আমি প্রায়ই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। কখনো কখনো আমি ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকি। জানি, এই রাগ প্রকাশ হতে না দিলে এটা বিস্ফোরিত হতে পারে। আমার ভয় হয়, আমি একবার কান্না শুরু করলে আর বুঝি বন্ধ করতে পারব না। নিজের এসব অনুভূতি আমি নিজের ভেতরেই লুকিয়ে রাখি। যেসব লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তারা মনে করেন আমি বুঝি তাদের দেখা সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ। আমি আমার অন্তর্গত ক্ষতগুলোকে এতটাই লুকিয়ে রাখি।
কিন্তু ডাবলিনে এসে বুঝি আর পারলাম না। যখন আমি ১৩ শ’ শ্রোতার সামনে কথা বলার জন্য দাঁড়ালাম, তখন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না। আমার চোখের পানি কোনো বাধাই মানছিল না। জলভরা চোখ নিয়েই আমি বলতে শুরু করলাম, ‘উত্তর কোরিয়া একটি কল্পনাতীত দেশ। এটি এমন দেশ, যে দেশে বেআইনিভাবে বিদেশে একটি টেলিফোন করার জন্যও প্রাণদণ্ড হতে পারে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মা একবার আমাকে বলেছিলেন, ফিসফিস করে কথা বলো না। পাখিরা, ইঁদুররাও তোমার কথা শুনে ফেলতে পারে।’
বলতে বলতে আমার দু’চোখের পানি গাল বেয়ে পড়তে লাগল। বললাম, ‘যেদিন আমরা উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে চীনে ঢুকি, সেদিন এক চীনা দালাল মাকে ধর্ষণ করে। সে পরে আমার সাথেও একই কাজ করে। এভাবে উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে আসা ৭০ শতাংশ নারী চীনাদের হাতে ধর্ষিত হয়। কোনো কোনো সময় তারা এসব নারীকে সামান্য দুই শ’ ডলারের বিনিময়ে বিক্রিও করে দেয়। … আমরা যখন গোবি মরুভূমি পার হচ্ছিলাম, তখন আমি মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিলাম বিস্মৃত হওয়াকে। কিন্তু আজ তোমরা আমার কথা শুনছ, আমার কথা ভাবছ এটা আমার বিরাট প্রাপ্তি।’
আমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতারা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারা কাঁদছিল। আমি চার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম এবং ভাবলাম, ন্যায়বিচার এখনো আছে এবং এই হলরুমেই আছে। তবে আমাকে আরো একটি মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে। ওই সম্মেলনের পর আমাকে কয়েক ডজন সাক্ষাৎকার দিতে হয়। আমার মনে হয়, পালিয়ে আসার কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ বাদ দেয়ার মধ্য দিয়ে আমি যে পাচার হয়ে এসেছিলাম তা লুকাতে পেরেছি। তা হোক, মূল বিষয়টা যদি ঠিকভাবে বলে থাকি তাহলে খুঁটিনাটির এত কী কাজ!
ডাবলিন সম্মেলনের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আমি এই স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করি। তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, নিজ দেশ এবং পালানোর পথে চীনে যা ঘটেছে তা যদি আমি যথার্থভাবে প্রকাশ না করি, তা কি ঠিক হবে? এ অবস্থায় একদিন সিউলে মা, বোন ও আমি কথা বলছিলাম। চীনে আমাদের ওপর যা ঘটেছিল তা আমরা কোনো দিন আমার বোনকেও জানতে দিইনি। এখন যদি ওসব কথা বইতে লিখি, তাহলে কী হবে? সত্যি বটে, দক্ষিণ কোরিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এদেশে বুলেট ট্রেন আছে, আধুনিক স্থাপত্যের অনেক স্থাপনা আছে। কিন্তু পারিবারিক ধ্যানধারণা এখনো পুরনো দিনের মতোই। তাই এদেশের লোকজন যখন জানবে টিকে থাকার জন্য আমরা কী করেছি, তখন কেউই আমাদের আর আগের মতো একই চোখে দেখবে না। তাহলে?
এবার এগিয়ে এলেন আমার মা। আমাদের জীবনে যা ঘটেছে তা হুবহু তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দিলেন তিনি। বললেন, ‘সারা দুনিয়াকে জানাতে হবে যে, উত্তর কোরিয়া একটি বড় বন্দিশালা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের নারীরা চীনে যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহায়, সে কথা মানুষকে জানাতে হবে। যদি তুমি তাদের কথা না বলো, তাহলে কে বলবে, বলো?’ মায়ের সাথে একমত হলো আমার বড় বোনও।
সিদ্ধান্ত নিলাম, যা ঘটেছে সবই লিখব। যেইমাত্র এ সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজেকে প্রথমবারের মতো মনে হলো একজন মুক্ত মানুষ। এতদিন মনে হতো, আমার ওপর ভারী আকাশটা চেপে বসে আমাকে মাটির সাথে পিষে ফেলতে চাইছে। সেটি এখন সরে গেছে। আমি এখন বুকভরে শ্বাস নিতে পারছি।
মূল : ইয়নমাই পার্ক
অনুবাদ : হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী