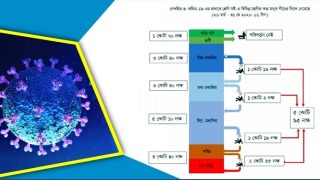অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনবিষয়ক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক বিভক্তি, মেরুকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে টানাপড়েনের সূত্রপাতের কারণে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত এক সময় হিসেবেই উন্নত বিশ্ব ২০১৭ সালকে স্মরণ করবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক কর্মসক্ষমতা দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বলয়গুলোকে হটিয়ে দেয়া অনেকটাই অসম্ভব। যদিও বাজার ও অর্থনীতি এখনো রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বল্পমেয়াদি সমস্যার ঝুঁকিগুলোও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।
একমাত্র যুক্তরাজ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যারা এখন ব্রেক্সিট প্রক্রিয়ার ফলে বিশৃঙ্খল ও বিভেদমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন। এছাড়া ইউরোপের অন্য স্থানে জার্মানির গুরুতরভাবে দুর্বল চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল একটি জোট সরকার গঠন করার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করছেন। এর কোনোটিই যুক্তরাজ্য কিংবা ইউরোপের জন্য ইতিবাচক নয়; বরং এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংস্কারের লক্ষ্যে ফ্রান্স ও জার্মানির হাত মেলানো। সবচেয়ে বড় ধাক্কা হিসেবে যে বিষয়টি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হলো, আর্থিক কঠোরতা। উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অদম্য সমন্বয়ী আর্থিক নীতির ক্রমাগত ওলটপালট খুব একটা কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয় না। সম্ভবত অর্থনৈতিক মূলনীতিগুলোর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঊর্ধ্বমুখী সমকেন্দ্রিকতা বা একই কেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা অনুমোদিত বাজারমূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে তা নাগালের মধ্যে রাখে।
যেমন— এশিয়ায় ভারসাম্যহীন অবস্থার বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গ্রহণের কারণে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন। ভারতও তার প্রবৃদ্ধি ও সংস্কারের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এ দেশগুলোর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর অবস্থান কী হবে কিংবা তারা কি তুলনামূলকভাবে ভারত ও চীন থেকে পিছিয়ে পড়বে?
প্রযুক্তি প্রসঙ্গে যদি বলা হয়, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোয় চীন ও যুক্তরাষ্ট্রই কর্তৃত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধারাবাহিকভাবে তারা তহবিল গঠন করছে। দেশ দুটি অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার উর্বর স্থান হিসেবে চিহ্নিত। এর মধ্যে রয়েছে সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক অগ্রসরতা ও ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রক্রিয়াগুলো।
এ ধরনের প্লাটফর্ম তৈরি কেবল নিজেদের জন্য লাভজনক নয়; বরং বিজ্ঞাপন, বণ্টন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চারপাশের পরিচালিত নতুন ব্যবসার মডেলগুলোর জন্যও উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।
এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদাহরণ টানা যেতে পারে। যেখানে অর্থনৈতিক কারণে এ ধরনের প্লাটফর্ম গড়ে ওঠার ঘাটতি রয়েছে। যেখানে লাতিন আমেরিকায়ও তাদের নিজস্ব ই-কমার্স প্লেয়ারস ‘মারকাডো লিবরে’ ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ‘মারকাডো পাগো’র মতো প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন রয়েছে।
বতর্মান বিশ্বে মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন। দেশটির বেশির ভাগ মানুষই চেক কিংবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বদলে মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইনে পেমেন্টের দিকে ঝুঁকেছে। ফলে চীনের আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।
সম্প্রতি দেশটির বার্ষিক উত্সব “সিঙ্গেল’স ডে” উপলক্ষে চীনের তরুণ ভোক্তারা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে যে পরিমাণ কেনাকাটা করে, তা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কেনাকাটার ইভেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ওই দিন চীনের সবচেয়ে বড় অনলাইন পেমেন্ট প্লাটফর্ম ‘আলিপে’ শক্তিশালী ক্লাউড কম্পিউটিং আর্কিটেকচার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ২ লাখ ৫৬ হাজার লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আলিপে প্লাটফর্মের মধ্যে রয়েছে ঋণ মূল্যায়ন, বীমা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সেবাও। তাছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রমগুলো ভালো চলছে।
আগামী বছরগুলোয় উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোকে নিজেদের সমন্বিত গ্রোথ প্যাটার্নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এখানে আমার প্রত্যাশা, জাতীয় সরকার হয়তো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে ঔপনিবেশিক সরকার, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শিক্ষাগত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিভক্তির ফলে প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলো এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে।
এর মধ্যে কিছু বিভক্তিকরণের মাত্রা অনেক বেশি তীব্র হতে পারে। অটোমেশন বা পণ্য উত্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো স্থায়ীকরণের প্রস্তুতি চলছে, এমনকি শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের দিকেও জোর দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মীরা যদি কাঠামোগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার সময় বড় ধরনের সমর্থন জুটিয়ে নিতে সক্ষমও হন, তা সত্ত্বেও শ্রমবাজারের অমিলগুলো বৃদ্ধি পাবে। বৈষম্যগুলো স্পষ্ট হবে। এটি পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক মেরুকরণে ভূমিকা রাখবে। তবে এখনো সাবধানতা অবলম্বন করে আশাবাদী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
প্রথমত. অপেক্ষাকৃত একটি মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উন্নত বিশ্বে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে।
এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের নাম। এখনো স্পষ্ট নয় যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে চায়, নাকি শর্তগুলোকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে সুবিধা পেতে চায়।
তবে বর্তমান অবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর বিশ্বের কাছে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিকাশমান নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার রূপকার হিসেবে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে বলা যেতে পারে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যারা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করেছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনকে ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে জলবায়ু সম্মেলন। যদিও ফেডারেল গভর্মেন্টকে ছাড়াই দেশটির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি, মেয়র, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা জলবায়ুবিষয়ক নীতিগুলো পালন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে।
সামনে এখনো অনেক পথ বাকি। বিশ্বজুড়ে কয়লানির্ভর জ্বালানি উত্পাদনের মাত্রা বাড়ছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস প্রতিবেদন করেছে, আগামী ১০ বছরে ভারতে কয়লা চাহিদা সবচেয়ে বেশি হবে। দেশটির ন্যূনতম প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে এ চাহিদার পরিমাণও বাড়তে থাকবে। তবে দৃশ্যের উল্টো পাশে কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে। আর তা হলো, খরচ কমানোর জন্য বিশ্ব দ্রুতগতিতে সবুজ জ্বালানির দিকে ঝুঁকবে।
এ বিষয়গুলো নির্দেশ করে, কয়েক মাস বা কয়েক বছরের ব্যবধানে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নামতে হবে। ভবিষ্যতের আবছা পটভূমিতে যে দৃশ্যটি কল্পনা করে আতঙ্কিত হতে হয় তা হলো, পর্বতসম ঋণের বোঝা। দৃশ্যটি এখনই বাজারের স্নায়ুচাপ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যা একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত অভিঘাতের মাধ্যমে সিস্টেমের দুর্বলতা বৃদ্ধি করে। তবে ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ার প্রক্রিয়াগুলোও ধারাবাহিক। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে চাকরি, আয়, রাজনীতি কিংবা সামাজিক মেরুকরণ— এ ধরনের কোনো আকস্মিক পরিবর্তন বা সুস্পষ্ট আলোড়ন ছাড়াই অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে অগ্রসর হবে।
লেখক: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক
ভাষান্তর: রুহিনা ফেরদৌস